পাইরেসি কেন বাড়ছে? আসলেই কি এটা চুরি, আর হঠাৎ কেন এত আলোচনা?

মোঃ মাসুদ রানা
প্রকাশঃ ২০ আগস্ট ২০২৫, ২:৪৫ পিএম
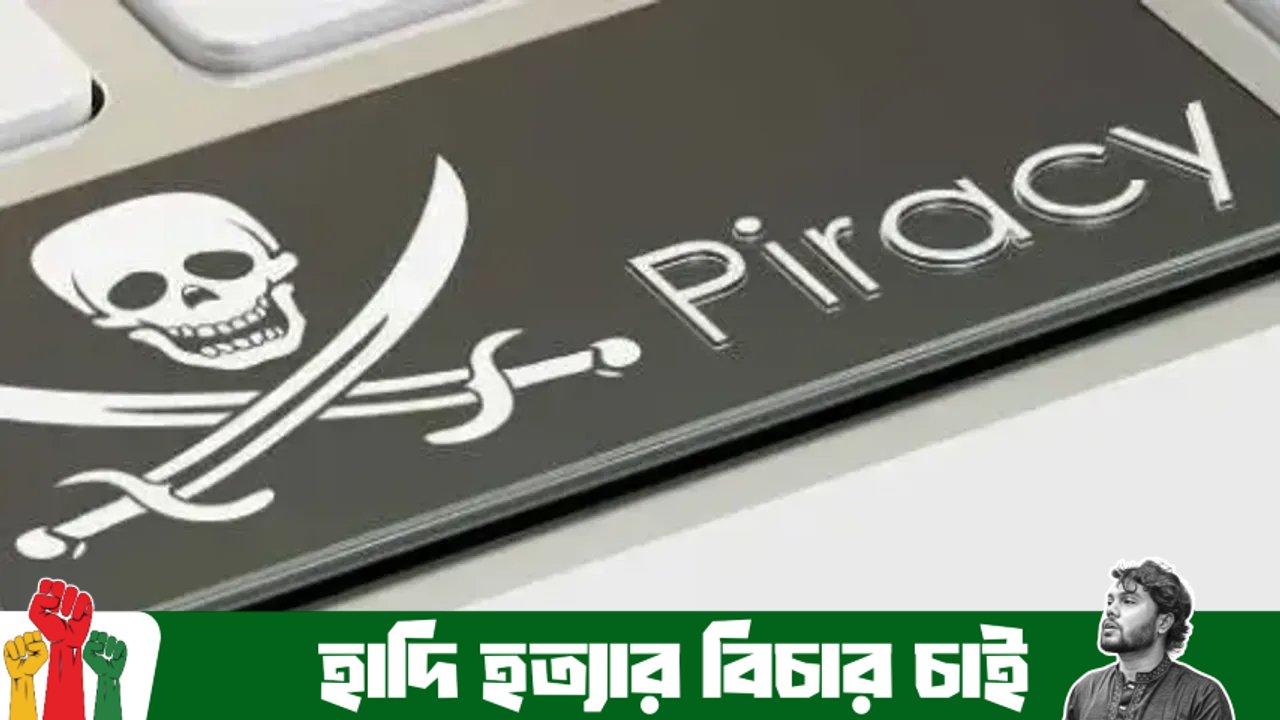
ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি লাইন খুব ঘুরছে—“If buying isn’t owning, pirating isn’t stealing.” যাকে সহজ বাংলায় করলে দাঁড়ায়, “যদি কিনেও জিনিসটা পুরোপুরি তোমার না হয়, তাহলে কপি করাকে কি চুরি বলা যায়?” এই কথাটা অনেকের মনে জমে থাকা রাগের সহজ প্রকাশ। রাগটা কিসের? মূলত মালিকানা (ownership) হারানোর ভয়, আর সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক সিস্টেমের ক্লান্তি। আবার ঐ লাইনকে আমরা মূলত একধরনের প্রতিবাদ হিসেবেও ধরতে পারি। কেনো? কারন আমরা যখন একটি বই, গেম বা মুভি কিনি। তখন সেটা আমাদের নিজের হওয়া উচিত। কিন্তু ডিজিটাল দুনিয়ায় সেটা হচ্ছে না। আমরা কেবল “লাইসেন্স” কিনছি, যেটা যেকোনো সময় কোম্পানি কেড়ে নিতে পারে।
একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক, ধরো তুমি একসময় একটি ডিজাইন টুল বা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার একবার কিনে বছরের পর বছর চালাতে। কিন্তু এখন একই কাজ করতে মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। প্রথম মাসে দাম সহনীয় মনে হলেও কয়েক বছর পর টের পাও মোট খরচটা পুরোনো এককালীন লাইসেন্সের চেয়েও বেশি হয়ে গেছে। সবচেয়ে ব্যাথাময় জিনিসটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন বন্ধ করলেই টুল বন্ধ। তুমি যে ফাইলগুলো বানিয়েছিলে, সেগুলো খোলা নিয়েও ঝামেলা শুরু, অনেক সফটওয়্যার বা টুলস ওপেনই করতে দেয় না। ব্যবহারকারী তখন স্বভাবতই ভাবে, “আমি তো টাকা দিলাম, কিন্তু জিনিসটা কি সত্যিই আমার হলো?”
এ রাগকে আরও বাড়িয়ে দেয় ডিজিটাল মালিকানার অস্পষ্ট নিয়ম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আসলে পণ্য কিনি না, কিনি ব্যবহার করার লাইসেন্স। কোম্পানি চাইলে শর্ত বদলাতে পারে, সার্ভার বন্ধ করলে কিছু ফিচার চলে যায়, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বেচাকেনার পরেও কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলা হয়। ২০০৯ সালে ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল: অ্যামাজন ভুলবশত বিক্রি হওয়া জর্জ অরওয়েলের 1984 ও Animal Farm–এর কপি বহু কিণ্ডল ডিভাইস থেকে দূর থেকে মুছে দেয়। ব্যাপারটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়, পরে অ্যামাজন ক্ষমা চায় ও আইনি সমঝোতাও করে। আর এই ঘটনাটি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিল ডিজিটাল কোনো কিছু কেনা মানেই সবসময় নিজের নয়। সেই সাথে মুভি বা সিরিজ দেখতে গেলে একাধিক প্লাটফর্মের সাবক্রিপশন কেনার পেইন সেটা বলার বাহিরে। কারণ সব মুভি বা সিরিজ এক প্লাটফর্মে থাকেই না।
ডিলিস্টিং
কখনো কখনো গেম, সিনেমা বা সিরিজের লাইসেন্সের মেয়াদ, মিউজিক রাইটস, বা পার্টনারশিপের শর্তের কারণে হঠাৎ করেই স্টোর থেকে উধাও হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় ডিলিস্টিং। উদাহরণ হিসেবে ২০২৪ সালে Forza Horizon 4–কে ধরা যায়। ডিসেম্বর-১৫ এর পর থেকে গেমটি আর মাইক্রোসফট স্টোর বা স্টিমে নতুন করে কেনা যায়নি। যারা আগে কিনে রেখেছিল তারা খেলতে পারলেও, নতুন ক্রেতার জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলো মানুষকে মনে করায় ডিজিটাল কন্টেন্ট দোকানে থাকলেই কেবল বাস্তব, দোকান বদলালে বা দরজা বন্ধ হলে তোমার অধিকার”ও ফিকে হয়ে যেতে পারে।
কেন পাইরিসি চুরি নয়?
মাইনক্রাফট গেমটির নির্মাতা হলেন মার্কাস পার্সন, যিনি "নচ" নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বহু আগেই গেম ডেভেলপার্স কনফারেন্সে বলেছিলেন, পাইরেসি চুরি নয়। কারণ চুরিতে মূল বস্তুটা হারায়, আর কপিতে কেবল সংখ্যাটা বাড়ে। তার যুক্তি ছিল এই কপিকারীদের অনেকেই সামর্থ্য ও সুবিধা পেলে পরে বৈধভাবে কিনবে। তাই পাইরেসিকে পুরোপুরি শত্রু হিসেবে না দেখে ভবিষ্যৎ গ্রাহক হিসেবে ভাবা যেতে পারে। এই বক্তব্য নিয়ে মতভেদ থাকলেও মালিকানা নিয়ে মানুষের হতাশা ও বাজারের বাস্তবতা বুঝতে এটা একটা ভালো উদাহরণ।
তাহলে কি পাইরেসি নরমাল?
এখানেই নৈতিকতা ও বাস্তবতার টানাপোড়েন। একদিকে পাইরেসি নির্মাতা, শিল্পী, ডেভেলপার থেকে শুরু করে সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তুমি যখন কোনো ইন্ডি ফিল্মমেকারের সিনেমা টরেন্ট বা কোনো অবৈধ উপায়ে কোনো থার্ড-পার্টি সাইট থেকে নামাও। এতে সিনেমার ফিল্মমেকারদের পরের সিনেমার বাজেটটা হয়তো অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, যখন ব্যবহারকারী দেখে যে নিজের টাকায় কেনা ই-বুক দূর থেকে মুছে দেওয়া যায়, বা প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হলে গেমেই ঢোকা যায় না, তখন তার মাথায় প্রশ্ন ওঠে “আমি যে কিনেছিলাম, আমার নিজেরটা কোথায়?” এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় ওই ভাইরাল লাইনের মতো প্রতিবাদের ভাষা—“If buying isn’t owning…” এটা কেউ কেউ পুরোপুরি ন্যায্যতা হিসেবে ব্যবহার করে, আবার কেউ দেখায় কোম্পানিগুলোর প্রতি চাপ সৃষ্টির স্লোগান হিসেবে।
বাস্তবটা হলো পাইরেসি কোনো রোমান্টিক বিদ্রোহ নয়। তেমনি কেবল পুলিশ কড়া করলে বা ডিআরএম শক্ত করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। পাইরেসির বড় অংশই Value VS Friction (ভ্যালু বনাম ঘর্ষণ) এই দুইয়ের লড়াই। যখন বৈধ উপায়ে সহজ উপায়ে, কম দামে, অফলাইনে ব্যবহার করা যায়, রিফান্ড থাকে স্বচ্ছ। তখন পাইরেসির পরিমানও কম থাকবে। আর যখন কিনে রেখেও নিয়ন্ত্রণ কম, অঞ্চলভেদে দাম অযৌক্তিক, লঞ্চের দিনেই ৫০ জিবি প্যাচ না দিলে গেম অপেন-ই হয় না। তখন ব্যবহারকারী মানসিকভাবে হতাশ হয় এবং পাইরেসির দিকে ছুটে।
সমাধান কি?
ধরা যাক, তুমি বাংলাদেশ/ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো, পকেট মানি সীমিত। একই সফটওয়্যারের যদি একটা স্টুডেন্ট/রিজিওনাল প্রাইস থাকে, আর পাশাপাশি একবার দিলেই চিরকালের লাইসেন্স- তাহলে তুমি হয়তো সাশ্রয়ী দাম দিয়ে বৈধটাই নেবে। আবার একটি গেম স্টোর যদি তোমাকে বলে, “আমরা তোমাকে অফলাইন ইনস্টলার দিচ্ছি, প্রয়োজন হলে ব্যাকআপ রেখো। ভবিষ্যতে আমাদের সার্ভার নেমে গেলেও মূল গেমটা তোমার” তাহলে তোমার নিরাপত্তাবোধ বাড়বে। সিনেমা/ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যদি স্পষ্ট করে দেয় “ক্যাটালগ থেকে শিরোনাম নামালে আগে জানাবো, বিকল্প অ্যাক্সেস দেবো, বা দাম সমন্বয় করবো” তাহলে ব্যবহারকারীর আস্থা থাকে। আর রিফান্ড যদি বোতামের এক ক্লিকে, সময়মতো ফেরত আসে। তাহলে কেউ টরেন্টে যাওয়ার আগে দু’বার ভাববে। গুগল স্টাডিয়া বন্ধের সময় গুগল যে কেনাকাটা রিফান্ড করেছিল। এটা ঠিক সেই আস্থারই একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন উদাহরণ, যদিও প্ল্যাটফর্ম নির্ভর গেমিংয়ের ঝুঁকি একদমই বাদ দেওয়া যায় না।
আমার ব্যক্তিগত মতামত
আমি পাইরেসিকে সমর্থন করি না। এটা শেষ পর্যন্ত সৃজনশীল মানুষদেরই ক্ষতি করে। যাদের পরিশ্রমে আমরা গেম খেলি, গান শুনি, সফটওয়্যার ব্যবহার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে অনেক সময় ব্যবসায়িক মডেলগুলো ভোক্তাকে মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে। আর সেখান থেকেই ক্ষোভ, মিম, প্রতিবাদ এবং অবশেষে পাইরেসির নৈতিক গ্রে এরিয়া (সাদা ও কালোর মিশ্রণ) তৈরি হয়। কাজেই সমাধানটা আইনশৃঙ্খলা দিয়ে নয়, বরং Increase value, reduce friction (ভ্যালু বাড়াও, ঘর্ষণ কমাও) এভাবে সমাধান করা উচিত। ন্যায্য দাম, লাইফটাইম লাইসেন্স বা অন্তত যুক্তিযুক্ত পারপেচুয়াল অপশন, অফলাইন অ্যাক্সেস, কম ডিআরএম, স্বচ্ছ রিফান্ড, আর কনটেন্ট ডিলিস্টিং এর আগে পরিষ্কার নোটিশ - এগুলো যত বাড়বে, পাইরেসির যুক্তি তত ক্ষীণ হবে। সেই সাথে পাইরেসিও কমতে থাকবে।
কফিপোস্টের সর্বশেষ খবর পেতে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল অনুসরণ করুন।
© কফিপোস্ট ডট কম
অনলাইনে পড়তে স্ক্যান করুন